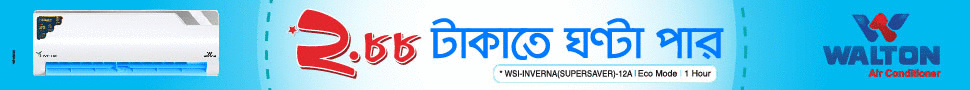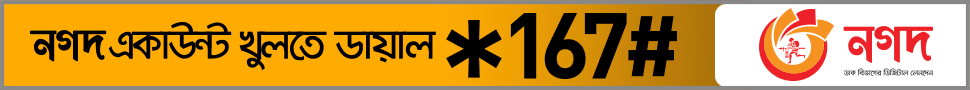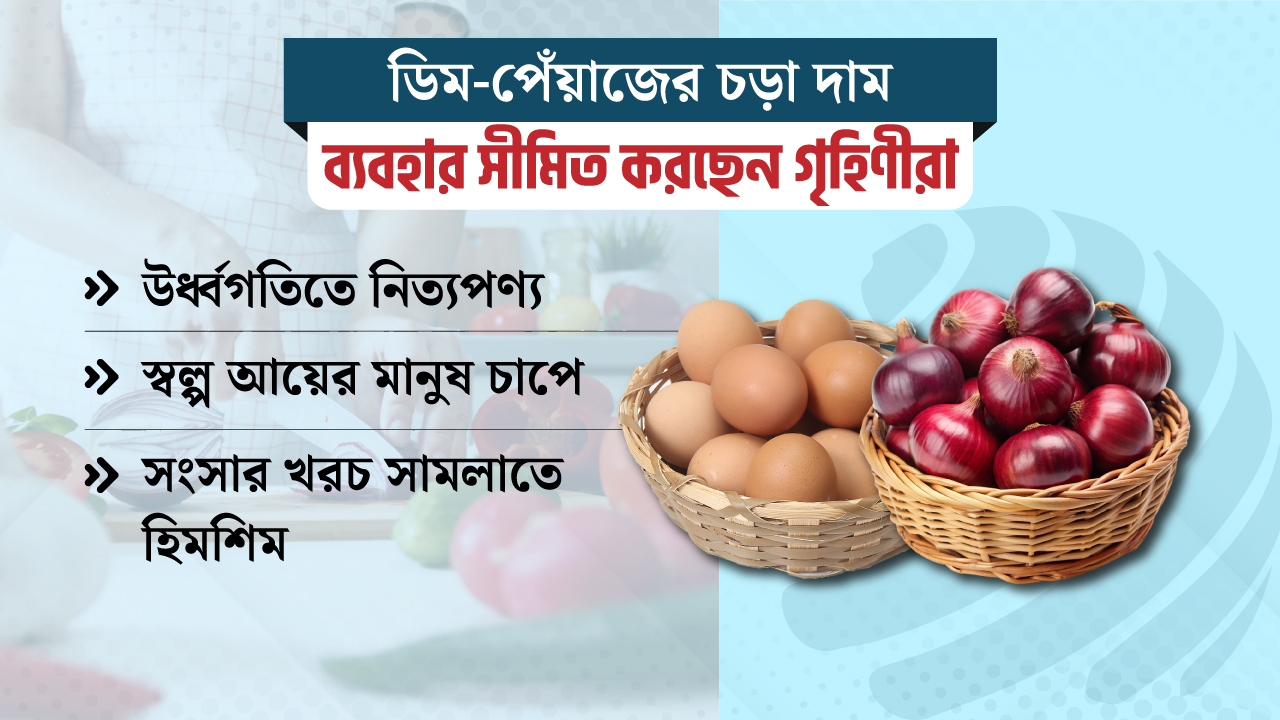বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র নতুন কৃষি সম্পর্ক
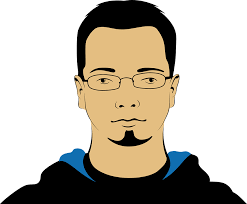
- আপডেট টাইম : রবিবার, ২৪ আগস্ট, ২০২৫
- ২ বার পঠিত
বিডি ঢাকা ডেস্ক
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক বর্তমানে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে তৈরি পোশাক শিল্পকে বাঁচানোর কৌশল, অন্যদিকে খাদ্যনিরাপত্তা ও স্থানীয় কৃষির অস্তিত্বের প্রশ্ন- এই দুই প্রান্তের টানাপোড়েনেই গড়ে উঠছে সাম্প্রতিক সময়ের দুই দেশের বাণিজ্য সমীকরণ। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজার, যেখানে ২০২৪ সালে ৮৩৬ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। বিপরীতে আমদানি করেছে মাত্র ২২১ কোটি ডলারের পণ্য।
এর ফলে ৬১৫ কোটি ডলারের বিশাল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তৈরি হয়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা মেটাতে ওয়াশিংটন তৈরি পোশাকে ৩৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিলে, বাংলাদেশ একটি ‘মৌন চুক্তি’র মাধ্যমে মার্কিন কৃষিপণ্য আমদানির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে আপাতত পোশাক খাতের রপ্তানি সুবিধা অক্ষুণœ থাকলেও দেশের কৃষি ও অর্থনীতির ভেতরে নানা বিতর্ক ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই চুক্তির লাভ-ক্ষতি একেবারেই দ্বিমুখী।
একদিকে তৈরি পোশাক শিল্প রক্ষা পেয়ে বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ স্থিতিশীল থাকবে, অন্যদিকে উচ্চমূল্যের আমদানির চাপ বৈদেশিক রিজার্ভকে দুর্বল করবে। মার্কিন গম কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের তুলনায় ২০-৩০ শতাংশ বেশি দামে কিনতে হবে বাংলাদেশকে। একইভাবে তুলা ও বিমান কেনা সরাসরি উৎপাদনশীল নয়, বরং উন্নয়ন অগ্রাধিকারের বাইরে চলে যাবে।
নির্মোহ দৃষ্টিতে বলা যায়, এ ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিবর্তে প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস কিংবা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে সহযোগিতা বাড়ালে তা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ অনেক বেশি লাভবান হতো। বাংলাদেশকে এমনতর এক জটিল পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে কোনোভাবেই দায়ী করা যায় না। আসলে এর জন্য মূল দায় অন্যায্য ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদ ও আমলারা, যারা মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের শ্রমিক শোষণের হাতিয়ার হিসেবে সস্তা শ্রমের পোশাক খাতকে প্রণোদনা-করছাড় নামের দুধ-ভাত খাইয়ে মহীরুহ রূপ দিয়েছে।
অন্তর্বর্তী সরকার অনেকটা বাধ্য হয়েই যতটা সম্ভব কম ব্যথা দিয়ে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাটিকে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ কী পেল আর কী দিল, তা বুঝতে কিছু তথ্য-উপাত্তের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়। ব্রিটেনের লেস্টার শহরে বছর কয়েক আগে বিশ^খ্যাত ‘বুহু’ ফ্যাশনের কারখানাগুলোতে আধুনিক দাসত্বের অভিযোগ তদন্তকালে দেশটির জাতীয় অপরাধ সংস্থা বলেছে, এখানে অবস্থা ‘সত্যিই ভয়াবহ’। পোশাক ও বস্ত্রশিল্পের আতুড়ঘর ব্রিটেনে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি কী হতে পারে! এটি জানতে ব্রিটেনের ইউনির্ভার্সিটি অব নটিংহ্যাম এক গবেষণায় (২০২৫) দেখেছে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রপ্তানি সরবরাহ শৃঙ্খলে, বিশেষ করে সাব-কন্ট্রাক্টে ১০০ শতাংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক ও বেআইনি শিশুশ্রমিক; ৩২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক ন্যূনতম মজুরির চেয়েও কম বেতন পাচ্ছেন।
শ্রমিকদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সপ্তাহে ৬ দিন, দৈনিক ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করে। যদিও এই খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, তবে তারা পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় প্রতি মাসে গড়ে ২,০০০ টাকা (১৮ মার্কিন ডলার) কম আয় করে। তদারকির অভাবে শিশুশ্রম, কম বেতন, নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ ও নির্যাতন অত্যন্ত বেশি। ৫৬ শতাংশ কারখানার শ্রমিক তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্রে হুমকি বা নির্যাতনের শিকার এবং প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে ৬৮ শতাংশ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৯০ শতাংশই নারী।
ইউরোপীয় পরিবেশ সংস্থার মতে, ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক কেনাকাটায় জনপ্রতি প্রায় ২৭০ কেজি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্যবহৃত টেক্সটাইল পণ্য মোট ১২১ মিলিয়ন টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করেছে। বস্ত্রপণ্যে রং করা এবং ফিনিশিং প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সুপেয় পানির ২০ শতাংশ দূষণের জন্য দায়ী এবং একবার পলিয়েস্টারের পোশাক ধুলে তা থেকে ৭ লাখ মাইক্রোপ্লাস্টিক ফাইবার নির্গত হতে পারে, যা খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশে করে।
এমন একটি শিল্পকে রক্ষায় বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে দেশটির কৃষি খাতকে প্রণোদনা দেওয়ার যে কৌশল গ্রহণ করেছে, তা দেশের জন্য কতটা ফলদায়ী হবে তা ভবিষ্যৎই বলে দেবে। অথচ অতীতে দেখা গেছে চীন, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান ও আফ্রিকার কিছু দেশ এমন পরিস্থিতিতে পড়ে প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিনির্ভর খাতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তির মাধ্যমে নিজ দেশের প্রযুক্তি খাতকে অনেকটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, যার সুবিধা তারা ধীরে ধীরে পাচ্ছে।
বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে বিন্যস্ত হতে যাওয়া এই বাণিজ্য সম্পর্কে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম (জিএমও) নিয়ে বিতর্ক ও খাদ্যনিরাপত্তা এখন গুরুতর আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদ অন্তর্বর্তী সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘একটি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখিÑ এরই মধ্যে আমেরিকানদের সঙ্গে যত কথাবার্তা হয়েছে, তার মধ্যে তারা কৃষিতে জিএমও (জেনেটিক্যালি মোডিফায়েড অর্গানিজম) এনেই ছাড়বে।
আমার মন্ত্রণালয় যেহেতু কৃষি মন্ত্রণালয় না, এ বিষয়ে কিছু করতে পারছি না। কিন্তু আমেরিকানদের সঙ্গে যতই কথাবার্তা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছেÑ তাদের জিএমও আনার জন্যÑ কৃষিটাকে ওরা দখলে নিয়ে নেবে এবং কোম্পানিগুলো চলে আসবে।’ তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, মার্কিন গো-মাংসের মাধ্যমে হরমোন অবশিষ্টাংশ বা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সজনিত রোগ দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতোমধ্যেই মার্কিন জিএমও খাদ্যের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো জিএমও খাদ্যের দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যঝুঁকি নিরূপণের মতো পর্যাপ্ত গবেষণা সুবিধার ধারেকাছেও নেই।
পাশাপাশি আশঙ্কা করা হচ্ছে, জিএমও প্রযুক্তির মাধ্যমে মার্কিন কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে প্রভাব বিস্তার করবে, যা আমদানিনির্ভরতা বাড়াবে। এছাড়া যেহেতু বাংলাদেশ বর্তমানে গমের ৯০ শতাংশ ও তুলার ৭০ শতাংশ আমদানি করে, সেহেতু ভবিষ্যতে উচ্চমূল্যেও মার্কিন কৃষিপণ্য আমাদানি দেশের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
ওদিকে মার্কিন গরুর মাংস আমদানির প্রস্তাব ও চেষ্টা স্থানীয় খামারিদের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিয়েছে। কারণ প্রস্তাবিত দামে (প্রতি কেজি ৩৫০-৪০০ টাকা)। এটি স্থানীয় দামের (৮০০ টাকা) প্রায় অর্ধেক, যা দেশের প্রান্তিক খামারিদের, বিশেষত নারী উদ্যোক্তাদের, আয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত পতন ঘটাতে পারে। তবে দেশে মাংসের উচ্চমূল্যে পুষ্টিহীনতায়ও যে গুরুতর সংকট রয়েছে, সেটিও স্বীকার করতে হবে।
লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের কৃষি রপ্তানি খাতও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি আয় প্রায় ৫৯.৫৫ কোটি ডলারে পৌঁছেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ৯.৩১ শতাংশ বেশি। এটি তৈরি পোশাকের ওপর নির্ভরতা কমানোর সুযোগ সৃষ্টি করলেও কোল্ড চেইন ও অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবের অভাব, কনটেইনার ও বিমান ভাড়ার অতিরিক্ত খরচ এবং রপ্তানিতে নগদ প্রণোদনা ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করার মতো চ্যালেঞ্জ কৃষি রপ্তানি বৃদ্ধিকে সীমিত করছে।
ফলে জিএমও খাদ্যের ঝুঁকি মোকাবিলা, স্থানীয় কৃষি খাত সুরক্ষা এবং কৃষি রপ্তানির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো এখন বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের জন্য সমন্বিত একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এখানেও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বড় বাধা। টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়া, কনটেনার ও বিমান ভাড়ার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত হিমাগার ও ল্যাব সুবিধার অভাবে কৃষিপণ্য রপ্তানি তার সম্ভাবনার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের করণীয় স্পষ্ট।
প্রথমত, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও জাপানের মতো নতুন বাজারে কৃষি রপ্তানি বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়ত, জিএমও পণ্যের জন্য কড়া নীতিমালা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বাধ্যতামূলক লেবেলিং চালু করতে হবে। তৃতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি ও গবেষণায় সহযোগিতা চাইতে হবে। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো প্রান্তিক কৃষক ও খামারিদের সুরক্ষা দেওয়া, যাদের শ্রম ও উৎপাদন ছাড়া কৃষি খাত ও খাদ্যনিরাপত্তা কোনো দিনই টেকসই হবে না।
পরিশেষে বলা যায়, তৈরি পোশাক শিল্পকে রক্ষার তাগিদে গৃহীত এই কৃষি আমদানি চুক্তি বাংলাদেশের জন্য সাময়িক স্বস্তি হলেও দীর্ঘমেয়াদে বড় ঝুঁকি হিসেবে দেখা দিতে পারে। বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর চাপে খাদ্যনিরাপত্তা বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। বরং স্থানীয় কৃষিকে শক্তিশালী করা, প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করা এবং নতুন বাজার অন্বেষণ করাই বাংলাদেশের জন্য টেকসই সমাধানের পথ। এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা হলো স্বল্পমেয়াদি স্বস্তি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা ও কৃষি সার্বভৌমত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া।